১.
রাষ্ট্রের কাছে নিরাপত্তা পেতে হলে, ব্যক্তির প্রাইভেসিতে ছাড় দিতে হবে—এই ধারণা বেশ বাজার পেয়েছিল ওয়ার অন টেররের যুগের শুরুতে। যুক্তিটা এমন যে, রাষ্ট্র যদি সব সময় সবার ওপর নজরদারি করতে পারে, তাহলে সন্ত্রাসবাদীরা অঘটন ঘটাতে গেলে তাদের যথাসময়ে ঠেকিয়ে দেয়া যাবে।
কিন্তু যেই রাষ্ট্র গণনজরদারির এই যুক্তি তৈরি করল, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই একটা উদাহরণ পাবেন না যে এই গণনজরদারির কারণে কোনো টেররিস্ট অ্যাটাক ঠেকিয়ে দেয়া গেছে।
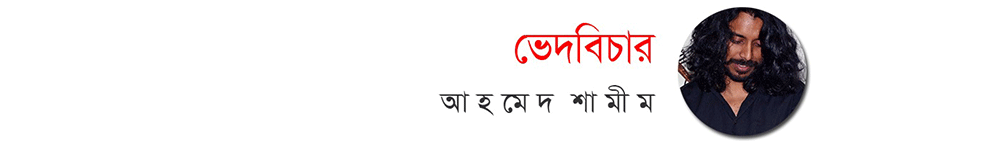 টেররিস্ট অ্যাটাক বাদ দেন, এই যে ঘন ঘন ম্যাস শুটিংয়ে সাধারণ মানুষ আর স্কুলের বাচ্চারা মারা যায়, গণনজরদারি তার কিছুই তো ঠেকাতে পারে নাই। এটা খোদ মার্কিন সরকার নিজে জানে, সিআইএ, এনএসএ’র রিপোর্টে তা স্বীকার করা হয়েছে।
টেররিস্ট অ্যাটাক বাদ দেন, এই যে ঘন ঘন ম্যাস শুটিংয়ে সাধারণ মানুষ আর স্কুলের বাচ্চারা মারা যায়, গণনজরদারি তার কিছুই তো ঠেকাতে পারে নাই। এটা খোদ মার্কিন সরকার নিজে জানে, সিআইএ, এনএসএ’র রিপোর্টে তা স্বীকার করা হয়েছে।
কারণ হিসেবে কথা উঠেছে যে, আপনি যখন নাগরিকের বিলিয়ন বিলিয়ন তথ্য জড়ো করবেন, তখন অসম্ভাবীভাবে ফোকাস হারাবেন। এমন কোনো মেশিন এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই যে সংগ্রহ করতে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে আপনাকে সন্ত্রাসী হামলা ঠেকাতে অগ্রীম সহযোগিতা করবে নির্ভুলভাবে। ফলে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সন্ত্রাসী হামলা হলেও, উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে নিরাপত্তার অজুহাত তুলে নাগরিকের প্রাইভেসিতে নজরদারি করার রাষ্ট্রীয় দাবিতে নাগরিকদের সায় পাওয়া যাচ্ছে না।
তবে আমেরিকার মত রাষ্ট্র গোপনে ঠিকই নাগরিকদের ওপর নজরদারি করছে, কেননা এই নজরদারির পেছনে আসল কারণ অন্য।
মজার ব্যাপার বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকের প্রাইভেসিতে রাষ্ট্রের সার্বক্ষণিক নজর রাখার অজুহাত হিসেবে এখনো নাগরিকের নিরাপত্তার দোহাইটাই দেয়া হচ্ছে। যদিও আদতে কারণটা আমেরিকার সেই গোপন কারণ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। সেই গোপনে আলো ফেলেই হুইসেল ব্লোয়ারগণ দেশদ্রোহীর মামলা খেয়েছেন। তাদের আলোকে আমাদের বর্তমানকে পর্যালোচনা করা যাক।
২.
নাগরিকের নিরাপত্তা বিষয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রেকর্ড খুব খারাপ। খুন ধর্ষণের মত চূড়ান্ত বিষয়গুলি এখন প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে গেছে। তারওপর যুক্ত হয়ছে ‘টেররিস্ট হামলা’র মামলা। ব্যাস, আমেরিকার ওয়ার অন টেররের আদলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রও বোধ করে বসল নাগরিকের ওপর গণনজরদারি দরকার। উন্নত বিশ্ব থেকে কিনে আনল হাইটেক সব আড়িপাতার যন্ত্রপাতি (খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত)।
আমাদের একটা ধারণা আছে যে এই প্রযুক্তি দিয়ে আসলে বিরোধী দলসমূহকে দমন পীড়নে রাখা হবে! তা অবশ্য ঠিক, এবং সেটা বর্তমান সরকারের নগদ লাভ। সরকার পাল্টালে তখনকার বিরোধীদল একই ফেরে পড়বে।
কিন্তু গণনজরদারি কেবল ক্ষমতালোভী দলগুলির এই ইদুর-বিড়াল খেলার খাতিরে না। আদতে গণনজরদারি এক বিশেষ সরকার বা একটি বিশেষ দেশের বিষয়ও না। পুরো নাগরিক সমাজকে নিও নিবারাল বিশ্ব বিন্যাসের ধামাধরা শাসকশ্রেণীর সামনে নতজানু রাখার একটা বৈশ্বিক চাল, দেশ বিশেষে বিবিধ ছল নিয়ে হাজির হচ্ছে।
একদেশদর্শী অভিজ্ঞতা দিয়ে এর স্বরূপ বোঝা যাবে না। তাই এই লেখায় বিশ্বপরিস্থিতির সাপেক্ষে কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ল।
৩.
ইতিহাস থেকে জানি, বর্তমান বিশ্ব বিন্যাসে রাষ্ট্রগুলি গোড়া থেকেই নতজানু নাগরিক-সমাজ চেয়েছে। ডিজিটালপূর্ব জগতে তা পেতে এতকাল তারা হিমশিম খেয়েছে কেননা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাগরিকগণ তাদের সেই জগতের অধিকারগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সচেতন। কিন্তু সেই চাওয়া এখন ডিজিটাল জগতে পূরণ হবার রাস্তা তৈরি হয়েছে সে জগতের নাগরিকগণের ওপর গণনজরদারির মাধ্যমে।
কেননা, নাগরিকের কর্মকাণ্ড যত ডিজিটাল হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার বর্ধিত রূপ হিসাবে ব্যক্তির ডিজিটাল সত্তা তৈরি হচ্ছে। এবং সেই ডিজিটাল ব্যক্তিসত্তার ওপর নজরদারি তত সম্ভবপর হয়ে উঠছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল ব্যক্তিসত্তার বাক-স্বাধীনতা, প্রাইভেসি, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ও চলে আসছে।
ফলে গণনজরদারি সম্পর্কে নাগরিকেরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্র আর নাগরিকের মধ্যে একটা দরকষাকষি চলছে বিষয়গুলি বোঝাপড়া এবং রফা করার ক্ষেত্রে। তাই ডিজিটাল জগতে নাগরিকের অধিকার নিরূপণ নিয়ে ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি। যেমন ধরেন, রাষ্ট্র আপনাকে বলে যে আপনি দুষ্কৃতকারী না হলে আপনার লুকানোর কিছু নাই। আপনি তখন বিপদে পড়ে যান, কেননা তখন প্রাইভেসির পক্ষে কথা বলা যেন দুষ্কর্মের পক্ষেই কথা বলা। আর আপনার সমাজ আর পরিবার নামক অণুরাষ্ট্র, পরমাণুরাষ্ট্রগুলিও রাষ্ট্রের যুক্তিকে সমর্থন করে।

দেখবেন, আমাদের সামাজিক পারিবারিক সংস্কৃতিতে প্রাইভেসিকে গোপনীয়তা হিসাবেই দেখা হয়, এবং গোপন হলেই সন্দেহের বস্তু, আর ‘নাথিং টু হাইড’কে ব্যাটাগিরি ইত্যাদি হিসাবে গণ্য করা হয়।
অতএব, রাষ্ট্রের কাছে প্রাইভেসি আপস করে বিনিময়ে নিরাপত্তা পাবার যুক্তির সামনে আপনি একা হয়ে পড়েন। কিন্তু একটু ভেবে দেখেন, প্রাইভেসি আদতে লুকানো বা গোপন করার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়।
এবার সে কথায় আসি।
৩.
ব্যক্তির প্রাইভেসি জিনিসটা আসলে কী?
দেখবেন, গণনজরদারির যুক্তির সমর্থনে রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রাইভেসি ধারণাটির গোপনীয়তা বা সিক্রেসির ব্যঞ্জনাকে হাইলাইট করে। সঙ্গে তুলে ধরে লুকানোর ধারণা—যেন আপনার কিছু জিনিস আপনি অন্যের কাছ থেকে লুকাচ্ছেন এবং আপনি যা লুকাচ্ছেন তা দুষ্কর্মের আকর আর আয়োজন।
এভাবে রাষ্ট্র প্রাইভেসির একটি পরোক্ষ ব্যঞ্জনাকে প্রধান করে আপনাকে দুর্বল করে আপনার প্রাইভেসিতে প্রবেশাধিকার চায়।
কিন্তু ব্যক্তির প্রাইভেসির প্রত্যক্ষ বা মূল অর্থ কিন্তু সেরকম নয়। প্রাইভেসির গোড়ায় হল ব্যক্তির এমন এক আওতা যেখানে অন্যের প্রবেশাধিকার ব্যক্তি নিজে সংরক্ষণ করেন। রাষ্ট্রে বা সমাজে ব্যক্তির প্রাইভেসি হল, ব্যক্তির প্রাইভেট প্রোপার্টি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি—সেখানে অন্যের প্রবেশ সার্বিকত নিষেধ, এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনুমতি সাপেক্ষ। বিশেষ শর্ত পূরণ করেই কেবল রাষ্ট্র বা অন্য কোনো পক্ষ ব্যক্তির প্রাইভেসি তথা প্রাইভেট প্রপার্টিতে প্রবেশ করতে পারে।
একদিকে দেখা যায়, ব্যক্তির প্রাইভেসিতে অন্য ব্যক্তির প্রবেশ ঘটে পারিবারিক কারণে, পেশাগত কারণে, বন্ধুত্বের মাধ্যমে, বৈবাহিক বা অমন সব চুক্তি ইত্যাদি মাধ্যমে। এবং এই প্রবেশগুলির সীমা আছে, আর প্রবেশকারীভেদে ওই সীমার তারতম্যও আছে।
অন্যদিকে তেমন দেখা যায়, রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রাইভেসিতে প্রবেশ করতে পারে, তবে তাও যথাযথ শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, অর্থাৎ চুক্তি মোতাবেক। যেমন ধরেন, ওই বিশেষ ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের সন্দেহ হয়েছে, রাষ্ট্র তার বিচার বিভাগ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রশাসনিক বিভাগ দিয়ে ওই বিশেষ ব্যক্তির ওপর নজরদারি করতে পারে। করেও আসছে এত কাল।
ধরেন আপনার ঘরে অবৈধ অস্ত্র আছে এই সন্দেহে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে আপনার ঘর তল্লাসি করতে পারে পুলিশ; আপনি সহযোগিতা করবেন এটাই রাষ্ট্রের সঙ্গে আপনার চুক্তি। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের এমন কোনো চুক্তি নাই যে সকলের ঘর সকল সময় রাষ্ট্রের নজরদারিতে থাকবে। এ ব্যাপারে আমরা সবাই কমবেশি সজাগ। কিন্তু ব্যক্তির ডিজিটাল সত্তা, এবং ডিজিটাল প্রাইভেসি সম্পর্কে আমরা এখনও খুব সচেতন তা কিন্তু না। কারণ বিষয়টা নতুন, এবং অ-ডিজিটাল জীবনের প্রাইভেসি ঠিক কীভাবে ডিজিটাল জীবনে অনূদিত হবে তা নিয়ে দরকষাকষি হচ্ছে। এই সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্র আপনাকে নজরবন্দি করতে চাইছে।
রাষ্ট্র চাইছে আপনার ডিজিটাল প্রাইভেসি বলে কিছু না থাক; আপনার ডিজিটাল জীবন সর্বদা সরকারের নজরদারিতে থাক। আগেই জেনেছি যে, এটা রাষ্ট্রের নতুন কোনো চাওয়া নয়। রাষ্ট্র আপনার অ-ডিজিটাল জীবনকেই নজরদারিতে রাখতে চায় এবং এই চাওয়া আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য টুল।
নাগরিককে শাসনে রাখার টুল এটা, রেজিমকে স্থায়িত্ব দেয়ার কার্যকরী টুল। এই টুল চালানোর জন্য যে লোকবল প্রয়োজন তা নিয়োগ দেয়া অসম্ভব এবং আত্মঘাতীও বটে। কিন্তু ডিজিটাল যুগে এসে তা সম্ভব হয়েছে, কারণ এখন আর অত লোকের দরকার নাই, মেশিনই পারে নাগরিকেরা কে কোথায় কী করছে, কার সঙ্গে কে মিশছে, কে কী কিনছে, কে কী দেখছে, কী খুঁজছে, কে কোথায় যাচ্ছে ইত্যাদি সব রেকর্ড রাখতে।
ফলে আপনাকে যদি বোঝানো যায় যে আপনার ডিজিটাল সত্তা আপনার জৈবিক সত্তা থেকে আলাদা কিছু এবং সেখানে আপনার প্রাইভেসি সরকারের সঙ্গে শেয়ারে রেখে আপনার সব সত্তার নিরাপত্তা পেতে পারবেন, তাহলে রাষ্ট্র নাগরিকের ডিজিটাল কর্মকাণ্ড নজরদারিতে রাখার মাধ্যমে নির্বিচারে রাষ্ট্রের সকল নাগরিককেই সন্দেহের আওতায় নিয়ে আসতে পারে। এর ফল খুব গভীর এবং সুদূরপ্রসারী।
নিও নিবারাল বিশ্ব বিন্যাস তার অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি কোনো চালেন্জকে দাঁড়াতে দেয় না। সেই লক্ষ্যে, কর্পোরেট পুঁজির এই বিন্যাসের পূজারি রাষ্ট্র তথা সরকারগুলির অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে দাড়িয়েছে জনগণকে সর্বদা তটস্থ রাখা।
গণনজরদারির মাধ্যমে ব্যক্তির প্রাইভেসি ভেঙে দিয়ে সে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। আপনি যখন জানছেন আপনার সকল ডিজিটাল কর্মকাণ্ড সরকার বসে বসে দেখছে, তখন আপনার মানসিকতায় এর প্রভাব পড়ছে।
একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, এখন সিদ্ধান্ত তৈরি থেকে শুরু করে সিদ্ধান্তের পুনর্মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়ন প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি অনেক বেশি কাতরতায় ভোগে—স্বকীয়তা, স্বাভাবিকতার আর নিজের কর্তাসত্তার অভাব বোধ করে।
ভেবে দেখুন, রিয়ালিটি শোর মধ্যে বসবাস করছেন আপনি। এই শোতে আপনার সকল কর্মকাণ্ড অন্যের নজরদারিতে আপনার প্রতিক্রিয়ার ফসল। দেখেন, রিয়ালিটি শো’র প্রডিউসার ডোনাল্ড ট্রাম্প যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রায় হয় হয় অবস্থা, এটা কোনো কাকতাল নয়। অবশ্য হিলারি হলেও এর অন্যথা হবে না। কেননা তারা সবাই বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্ববিন্যাসের চৌকিদার।
একটু ধ্যান দিলেই তাদের ফাঁকিটা আপনি ধরতে পারবেন। দেখেন, কর্পোরেট কম্পানিগুলি আমেরিকায় ব্যক্তির মর্যাদা-সুবিধা ভোগ করার অধিকার আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু কই, সরকার কি পারবে কর্পোরেটগুলার প্রাইভেসিতে প্রবেশ করতে?
পারে না।
সরকার দেখেন নিজে পাবলিক, মানে সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণ খোঁজখবর নিতে পারবেন; পাবলিক কথাটার মধ্যেই সেই অধিকার খচিত আছে। কিন্তু দেখেন সরকারগুলি তাদের প্রাইভেসি সম্পর্কে সহিংস।
যান সরকারের হাড়ির খবর জানতে। খুন হয়ে যাবেন, লাশটাও আপনার স্বজনেরা খুঁজে পাবে না। প্রাইভেট আর পাবলিক ধারণা পাল্টে গেছে। যারা পাবলিক তারা প্রাইভেসি রক্ষা করে যাচ্ছে, আর যারা প্রাইভেট তাদের প্রাইভেসিকে পাব্লিকের কাছে তুলে দিতে চাপ দিচ্ছে।
৪.
সান বার্নাডিনোর ম্যাস শুটিংয়ের ঘটনার কথাই ধরেন। একটি মুসলিম আমেরিকান পরিবার গুলি করে অনেকগুলি ‘আমেরিকান লাইফ’ হত্যা করেছে। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ঘাতকের লক করা আইফোনে এফবিআই প্রবেশ করতে চায়। তারা আপেল কোম্পানিকে বলল, আইওএসের এমন ভার্সন তৈরি করে দিতে যাতে একটা ব্যাকডোর থাকে এবং তা দিয়ে যাতে এফবিআই চাইলে যে কারো আইফোনে ঢুকতে পারে।
ম্যাকাফি ভাইরাস গার্ডের মালিক কিন্তু ঘাতকের সেই বিশেষ আইফোনটিতে এফবিআইয়ের প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিল। এফবিআই তা নিবে না। তাদের অনেকদিনের চাওয়া আইওএসের ভার্সনগুলিতে তাদের জন্য একটা ব্যাকডোর থাকবে। যাতে তারা আমেরিকার জনগণের ওপর গণনজরদারি বাড়াতে পারে।
এই চাওয়া হাসিল করার জন্য এমন একটা সেন্সিটিভ ঘটনাই চাইছিল এফবিআই। সান বার্নাডিনোর ম্যাস শুটিংয়ের ঘটনা সেই সুযোগ এনে দিল। আমেরিকার আইনে প্রিসিডেন্স বলে একটা বিষয় আছে। আপেল যদি আদালতের রায়ে রাজি হত, তাইলে সেটা প্রিসিডেন্স বা নজির হিসাবে দাঁড়িয়ে যেত, এবং সকল ফোন কম্পানিকে ওই রায় মানতে হত।
কিন্তু আপেল জানে মার্কিন জনগণ যদিও ওই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ কিন্তু শেষ বিচারে প্রাইভেসিকেই ওপরে রাখবে। তাই আসল ব্যবসাটা ওখানে। আপেল ব্যবসা না হারানোর জন্য এফবিআইয়ের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। ব্যবসায়িকগোষ্ঠী তাতে সমর্থন যোগায়, ফলে এফবিআই পিছু হটতে বাধ্য হয়।
সম্প্রতি তারা বলেছে আপেলকে ছাড়াই তারা ওই বিশেষ ফোনে ঢুকতে পারছে। তাহলে ওই ফোনে ঢোকার অপেরাটিং সিস্টেমে কেন এফবিআই ব্যাকডোর চেয়েছিল তা বুঝতে আমেরিকান জনগণ ভুল করে নি।
৫.
তো প্রাইভেসি তাহলে পশ্চিমে এত বড় একটা ব্যাপার। ইউরোপ মনে করে প্রাইভেসি হল মানবাধিকার। আমেরিকাদ্বয়ের মতে ব্যক্তির প্রাইভেসি বা প্রাইভেট প্রপার্টি ব্যক্তিরই সম্প্রসারণ।
সে বাবদে ডিজিটাল সম্প্রসারণকে ব্যক্তির ডিজিটাল সত্তা আকারে মানতে হবে। মানে, ডাটা আর কেবল ডাটা থাকছে না, তাও প্রাইভেট-পাবলিকে ভাগ হয়ে গিয়ে ব্যক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এখন নাগরিকের কোন তথ্য পাবলিক আর কোন তথ্য প্রাইভেট তা নাগরিকরাই ঠিক করেন, যেভাবে তারা ঠিক করেন কে সংসদে যাবে কে যাবে না। অর্থাৎ এটা ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে—ঐতিহাসিক দরকষাকষির মধ্য দিয়ে— নির্ণীত হয় রাষ্ট্রের বিধিবিধান—এটা একটা সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয় নয়—ঐতিহ্যিক সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও বিষয়।
আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। অন্যান্য বিশ্বে প্রাইভেসিকে যেভাবে ব্যক্তির মৌলিক বিষয় হিসাবে দেখা হয় পরিবার থেকেই তা আমাদের সমাজে সেভাবে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রাইভেসি জ্ঞান নেই এটা বলা ভয়ঙ্কর ভুল। ক্ষমতা যার হাতে সে কিন্তু সকল সমাজে প্রাইভেসির সুবিধা ভোগ করেছে। অবস্থাপন্নদের প্রাইভেসি তারা লাঠিয়াল দিয়ে রক্ষা করে। কেবল সর্বহারা কিংবা নিঃস্বদের বেলায় প্রাইভেসিটুকু বিলাসিতা।
গরীরের বাড়িতে হাতিরা যে কোনো সময় পাড়া দিতে পারে, হাতিদের বাড়িতে গরীবে গেইটের কাছেই দাঁড়িয়ে দরকার সারে। বাংলাদেশে গরীবের সংখ্যা বেশি তাই ধনীদের তাঁবেদার রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রাইভেসি নিয়া যা তা করার সাহস পায়। অথচ সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ হল জনগণের যে অংশ নিজের প্রাইভেসি রক্ষা করতে সমর্থ না, তাদের প্রাইভেসি নিশ্চিত করা। কিন্তু আমার সোনার বাংলায় সেই গণতন্ত্র কই!




